- অনুবাদ
- অভিধান
- আইন আদালত
- জোক্স
- আত্মজীবনী
- শিশুতোষ গ্রন্থ
- আবৃত্তি
- ইতিহাস ও সংস্কৃতি
- উপন্যাস
- জাতকের গল্প
- কবিতা
- কম্পিউটার
- কাব্যনাট্য
- চিকিৎসা
- চিত্রকলা
- ছোটগল্প
- জীবনী
- জীববিজ্ঞান/ভূগোল
- দর্শন
- দিনপঞ্জি
- ধর্ম
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান
- নাটক
- নারীবিষয়ক
- পরিসংখ্যান
- পাখি
- প্রবন্ধ
- ফোকলোর
- বিজ্ঞান
- বিবিধ
- বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী
- ভাষা ও ব্যাকরণ
- ভ্রমণ
- মনোবিজ্ঞান
- মুক্তিযুদ্ধ
- রচনাসমগ্র
- রম্য
- রান্না
- রূপচর্চা
- লোকসাহিত্য
- শিল্পকলা
- স্মৃতিকথা
- সংকলন
- ভৌতিক উপন্যাস
- সংগীত/স্বরলিপি
- গবেষণা
- গল্প
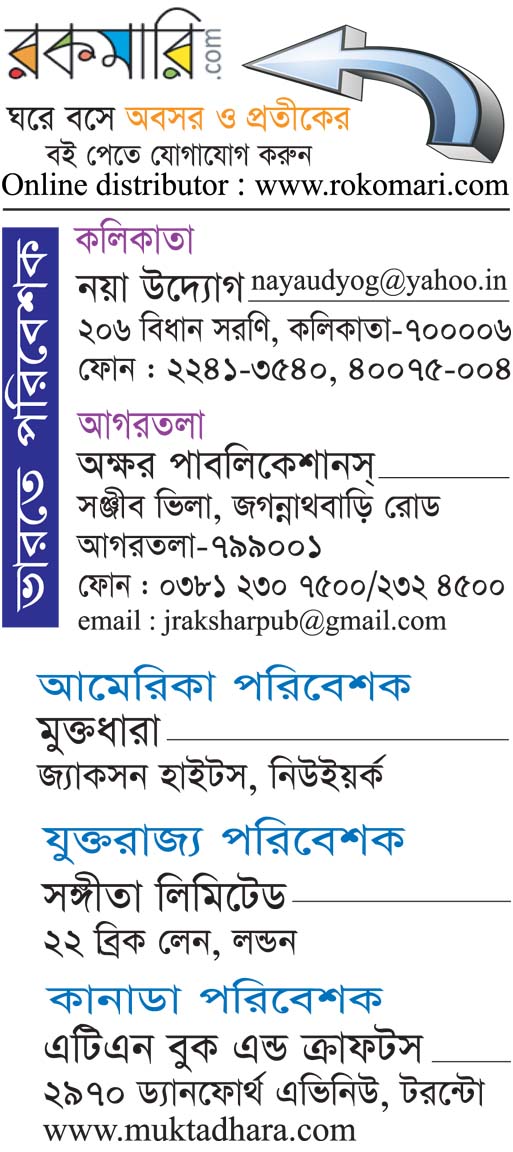
জন সাইটটি দেখেছেন
এবার তার নিজের বাসায় নিউ ইয়র্কের জামাইকাতে এবং আমাদের ডেনভারের বাসায় গত ফেব্রুয়ারিতে বেড়াতে এলে হুমায়ূনকে একাধিকবার শয়ন ঘরের নিভৃতিতে নামাজ পড়তে দেখেছি। কিন্তু যতদূর মনে হয়, প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচবার করে নামাজ তিনি পড়তেন না। অসুখের সময়টি ছাড়া ধর্মের ব্যাপারে তার মনোভাব কী ছিল কখনো জানার সুযোগ হয়নি। তবে লক্ষ্য করেছি, হাসপাতালে তার গলায় সার্বক্ষণিকভাবে লকেট দেওয়া হারের মতো একটা কিছু পরানো থাকতো, যার ধাতব লকেটের ভেতর আয়াতুল কুরসি লেখা রয়েছে।
যখন-ই ভাবি, মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে হুমায়ূন আহমেদ আসলেই এক জীবন্ত কিংবদন্তী। হুমায়ূনের সৃজনশীলতার ব্যাপ্তি ও বিন্যাস, এবং এর বিভিন্ন স্তরে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ
ও অবস্থানের কথা চন্তা করলে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। গল্প-উপন্যাস-নাটক-চলচ্চিত্রে সফল ও সিদ্ধহস্ত হুমায়ূন সংগীতের প্রতিও, বিশেষ করে আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকজ সংগীতের প্রতি, অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে পড়েন। সুযোগ পেলেই নাটকে, চলচ্চিত্রে, উপন্যাসে, এমন কি তার দৈনন্দিনের ঘটনা নিয়ে রচিত কলামেও সে ধরনের গানের কথা ঢুকিয়ে দিতেন। নিজে গান না গাইলেও গান শোনা, গান বোঝার মতো সজাগ ও পরিশীলিত কান ও মন তার ছিল।
কথা ছিল এবার নিউ ইয়র্কের বাৎসরিক বই মেলায় শুধুমাত্র এই দম্পতি হাজার বছরের বাংলা গানের ওপর একটি প্রামাণ্যগীতির অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন যেখানে ধারাবাহিকভাবে গান ও ধারা বর্ণনা দিয়ে এক ঘন্টার একটা মঞ্চ উপস্থাপনা হবে। পরিচালনা ও ধারা বর্ণনা করেবেন হুমায়ূন আর গান গাইবেন শাওন। আর এটি হবার কথা ছিল মূল মঞ্চে ৩০ জুন সন্ধ্যায় - অনুষ্ঠানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বাঞ্ছিত ‘প্রাইম টাইমে’। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেদিন সেসময় হুমায়ূন ছিলেন হাসপাতালের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে শায়িত। শুধু গানের অনুষ্ঠান নয়, সেদিন বিকেলে-ই তাঁর অঙ্কিত চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী হবারও কথা ছিল বইমেলাতে। হুমায়ূন সুযোগ পেলেই ছবি আঁকতেন। বেশিরভাগ ছবিই ল্যান্ডস্কেপ। দু’একটি পোর্ট্রেট। বিমূর্ত ছবি খুব একটা নেই। ছবি আঁকার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল হুমায়ূনের বরাবই-ই। আর ছিল রঙের বিন্যাসের প্রতি তার তীক্ষ্ম নজর ও গভীর উপলব্ধি। হুমায়ুনের ইচ্ছা ছিল তার পাঁচ বছরের পুত্র নিষাদ এই চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবে এখানে। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন ছবি যদি কিছু বিক্রি হয়, সম্পূর্ণ টাকাই দিয়ে দেবেন তার নিজের দেওয়া স্কুলটিতে, যার স্থপতি ছিলেন শাওন, এবং যার আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন বিশেষ কারণে তিনি তার চিত্রকলা বিক্রির পরিকল্পনা বাদ দিয়েছিলেন এবং বিদেশে তাঁর এই ছবিগুলোকে কেবল প্রদর্শনের জন্যেই টানাতে অনুমতি দেন, বিক্রয়ের জন্যে নয়। এছাড়াও, সেদিন-ই, ৩০ জুন শনিবার রাতেই, মুক্তধারার বইমেলার পক্ষ থেকে হুমায়ূনকে সম্মাননা দেবারও কথা ছিল সাহিত্য-শিল্পে তাঁর অসামান্য এবং সামগ্রিক অবদানের জন্যে। হুমায়ূনের হাতে সেই সম্মাননা তুলে দেবার কথা ছিল আমার। বলাবাহুল্য সেটাও আর ঘটে ওঠেনি। হুমায়ূন তখন গুরুতর অসুস্থ বেলভিউর আইসিইউ ইউনিটে। আর আমরা কয়েকজন ছিলাম তার পাশে।
অনেকেই হয়তো জানেন, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা ছাড়াও, হুমায়ূন পেশাদার যাদুকরের মতো করে অত্যন্ত চমৎকার ও উন্নত মানের জাদু দেখাতে পারতেন। তার পরিবেশনাও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কখনো কখনো তাৎক্ষণিকভাবে স্থির করে দু’একটা জাদু দেখিয়ে উপস্থিত লোকদের তাক লাগিয়ে দিতেন। এছাড়া আরেকটি ঝোঁক ছিল তার। দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে বসে খুব ধীর স্থিরভাবে নিবিড়চিত্তে দাবা খেলার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন হুমায়ূন। এখানে প্রধানত শাওন ও মাযহারের সংগে বসেই খেলতে দেখেছি তাকে। এমনকি হাসপাতালের বিছানায় শুয়েও। দাবায় তাঁকে হারানো সহজ কাজ নয়। আর তাই বোধ হয় উপযুক্ত সংগী খুব একটা খুঁজে পাননি তিনি এখানকার পরিচিত জনের মধ্যে।
হুমায়ূনের মতো অতিপ্রজ লেখকেরা সাধারণত অন্যের বই, অন্যের লেখা পড়েন না। কিন্তু এ ব্যাপারেও ব্যতিক্রমী ছিলেন হুমায়ূন। শুধু অনেক লিখতেন তিনি তাই নয়, দেখতাম প্রচুর পড়তেন-ও। দেশী-বিদেশী দুই সাহিত্য-ই। একবার আমাজনডটকম থেকে এক বাক্স উপন্যাস আর সায়েন্স ফিকশন কিনে আমাজনের মাধ্যমেই সরাসরি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাঁকে নিউ ইয়র্কের ঠিকানায়। মূলত নতুন বিদেশে আসা লেখকটির একাকিত্ব ঘোচাবার অভিপ্রায়েই, সেই সংগে তাঁর আসন্ন জন্মদিনের কথাটাও মনে ছিল। আট-দশ দিনের ভেতরেই অধিকাংশ বই পড়া শেষ করে ফেলেছিলেন হুমায়ূন। হাতের কাছে নতুন কোন বই পেলে, যার বিষয়বস্তুতে তার আগ্রহ রয়েছে, গোগ্রাসে পড়ে ফেলতেন তিনি। এতো দ্রুত পড়তে দেখে অবাক হয়েছিলাম আমি। কেননা আমার পড়তে অনেক সময় লাগে। দ্রুত পড়ার অভ্যেস গড়ে তুললেও বই বা ম্যাগাজিনগুলো যে আসলেই মনোযোগ দিয়েই আদ্যোপান্ত পড়েন হুমায়ূন, শুধু চোখ বোলান না, তা নানাভাবে টের পেয়েছিÑ একাধিকবার, উভয়ের পঠিত বই নিয়ে কথা বলতে যেয়ে ।
প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে ঘরে ভেতরে বা বাইরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কিংবা ঘাসের ওপর বসে অথবা খোলা নৌকোয় চড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে পছন্দ করতেন হুমায়ূন, নতুন নতুন জায়গায় ঘন ঘন বেড়াতে যেতেও। স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় নিয়ে নিজেও, অর্থাৎ পুরো হুমায়ূন পরিবার-ই পশ্চিমী পোশাক পরে খুব স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এসব সত্ত্বেও অনেক বিষয়ে হুমায়ূনের চিন্তাধারার মধ্যে অত্যাধুনিকতার বদলে সামাজিক গতানুগতিকতা মেনে চলা ও চলতি প্রথার প্রতি একধরনের সায় ও সম্মান প্রদর্শনের আভাস দেখতে পেয়েছি, যদিও ব্যক্তি জীবনে জীবনসংগী বেছে নিতে সামাজিক সকল রীতিনীতি ভেঙে দিতে দ্বিধা করেন নি। ধর্মের ব্যাপারে, ধর্মবিশ্বাস বা আচরণে, হুমায়ূনকে কিছুটা দোদুল্যমান মনে হয়েছে আমার। বাংলাদেশের প্রথাগত ও সামাজিক রীতি অনুযায়ী হুমায়ূন ও তার স্ত্রী শাওন দেখা হলেই বা ফোনে কথা বলার শুরুতেই আসসালামালাইকুম দিতে কখনো ভোলেন না। এ ব্যপারে আমি অবশ্য ওয়ালাইকুম সালাম বলার চেয়ে ‘কেমন আছেন’ বলে সম্ভাষণ জানাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। যেমনটা করি ‘নমস্কারের’ উত্তরেও। দৈনন্দিন জীবনে নমস্কার বা আসসালামালাইকুম বলা বা কেউ তা বললে একই ধরনের সম্ভাষণে প্রতিউত্তর দেওয়ার চাইতে সাধারণত ‘নিউট্রাল’ কোন শুভেচ্ছা বার্তা ব্যবহার-ই আমার বেশি পছন্দ। হুমায়ুনকে যখন কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাই, তখন তার শরীরে বাসা বেঁধেছে মারাত্মক এক ব্যাধি এবং স্ক্রিনিং-এর পর্যায়ে জানা গিয়েছে অনেক শক্তভাবেই নিজের অবস্থান গেড়ে নিয়েছে সেই রোগ। হুমায়ূন প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আমরা জানি জীবনের অনিশ্চয়তা যখন এতো তীব্র, আয়ুর দৈর্ঘ নিয়ে যখন লোকে এতো দুশ্চিন্তিত, তখনÑ মানে এরকম সময়ে, এই হতাশার দিনে মানুষ তৃণকুটাটি জড়িয়ে ধরেও বাঁচার চেষ্টা করে। বাঁচতে চায়। সাধারণভাবে ধর্মাচরণ করেন না, এমন অনেক মানুষও এই সময় মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে গিয়ে ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। হুমায়ূনকে আগে আমি কাছের থেকে দেখিনি। তাকে জানার সুযোগ ছিল না। ফলে ধর্মের ব্যাপারে তাঁর অবস্থানের কোন পরিবর্তন সাম্প্রতিককালে হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। তবে এবার তার নিজের বাসায় নিউ ইয়র্কের জামাইকাতে এবং আমাদের ডেনভারের বাসায় গত ফেব্রুয়ারিতে বেড়াতে এলে হুমায়ূনকে একাধিকবার শয়ন ঘরের নিভৃতিতে নামাজ পড়তে দেখেছি। কিন্তু যতদূর মনে হয়, প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচবার করে নামাজ তিনি পড়তেন না। অসুখের সময়টি ছাড়া ধর্মের ব্যাপারে তার মনোভাব কী ছিল কখনো জানার সুযোগ হয়নি। তবে লক্ষ্য করেছি, হাসপাতালে তার গলায় সার্বক্ষণিকভাবে লকেট দেওয়া হারের মতো একটা কিছু পরানো থাকতো, যার ধাতব লকেটের ভেতর আয়াতুল কুরসি লেখা রয়েছে। সেই হারটি, কালো মোটা সূতোয় মাঝখানে ধাতব লকেটে লেখা আয়াতুল কুরসি মৃত্যুর সময় পর্যন্ত শরীরে ধারণ করে ছিলেন হুমায়ূন। শাওন-ই খুব সম্ভত বেঁধে দিয়েছিল ওটা, তাঁর গলায়। প্রথম সার্জারীর পরে রিকোভারি রুমে ওটা হুমায়ূনের গলায় দেখতে না পেয়ে খুব-ই নার্ভাস লাগছিল শাওনকে। একাধিক জায়গায় অনুসন্ধান করে তবে সেটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। হুমায়ূনের কোন শুভাকাংখী ওটা তার গলায় ঝুলিয়ে দিলেও সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেটি পরিধানে কখনো কোন আপত্তি দেখিনি হুমায়ূনের। তাঁর জীবনাচরণের অন্যান্য দিক বিবেচনা করলে বোঝা যায় তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপারে খুব গোঁড়া ছিলেন না। ধর্মের সকল বিধি বিধান যে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন না, এটাও সহজেই বলা যায়।
ভালো খাওয়াদাওয়া এবং গুরুপাক মোগলাই খাবারের (নেহারী, তেহারী, বিভিন্ন ধরনের কাবাব, বিরিয়ানীসহ) দিকে তার যেমন ঝোঁক ছিল, তেমনি কাসুন্দি দিয়ে শাক, কিংবা সরষে ইলিশের বড় পেটি অথবা বেগুন ভাজা দিয়ে পাতলা খিচুড়ি খেতেও তার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। আর যা বা যতটুকুন খাবেন, তার সবটাই জ্বলন্ত চুলো থেকে সদ্য নামানো, তপ্ত ও টাটকা রাঁধা হতে হবে। তবে এক খাবার দুবেলা, বাসি খাবার অথবা সাদামাটা ভাত-ছোটমাছ-ডাল-শব্জি দিয়ে গতানুগতিক খাবার খেতে অনীহা ছিল তাঁর। আগ্রহ একেবারেই কম ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত কিংবা এক্সপেরিমেন্টাল খাবার খেতেও। পশ্চিমী রেষ্টুরেন্টে গিয়ে বড় বড় প্রিমিয়ার স্টেক কিংবা বিশাল প্লেটারে নানা জাতীয় সামুদ্রিক খাবারেও উৎসাহ দেখেছি তার। তবে কিমোথেরাপির জন্যে অরুচির কারণে পছন্দের খাবার-ও খেতে পারতেন না সব সময়। হুমায়ূনের খাবারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা ঝোঁকটা ছিল মূলত উচ্চবিত্ত মুসলমান পরিবারের অতিথি সমাবেশে দৈনন্দিন খাবারের মেনুর নমুনামাফিক। গরুর মাংস তার যেমন পছন্দ, মুরগী বা নিরামিষে তেমন নয়। এছাড়া বাজারের বড় কৈ মাছ, ইলিশ মাছ, কড়া করে রাঁধা শুটকী মাছ হুমায়ূনের বিশেষ পছন্দ।
হুমায়ূনের চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট তার বন্ধু-অন্ত প্রাণ। প্রিয় বন্ধুদের, সুহৃদদের অসুখে বিসুখে, বিপদে আপদে সাহায্যে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করতেন না হুমায়ূন। সংখ্যায় খুব বেশি বন্ধু তাঁর ছিল না, প্রচুর ব্যক্তিগত বন্ধুর প্রয়োজন-ও বোধ করেননি। কিন্তু একবার যাকে বন্ধু হিসেবে হৃদয়ে ধারণ করেছেন হুমায়ূণ, তাকে বরাবর আগলে রাখতে পছন্দ করতেন। মানবিক সম্পর্কের বেলায় আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে পার্থক্য তিনি করতেন না, যে ব্যাপারটায় আমার সংগে তার চিন্তার একাত্মতা আমাকে আলোড়িত করেছে।
আমাদের দেশের অনেকের মতো তাঁরো দুটি জন্ম তারিখ ছিল। একটা অফিসিয়াল- যেটা স্কুলে দেওয়া হয়েছিল। অন্যটি খাঁটি। স্কুলে দেওয়া জন্ম তারিখ-ই রয়েছে তাঁর পাসপোর্টে, যেটার কথা হুমায়ূণ প্রায়-ই ভুলে যেতেন। আমেরিকায় আবার জন্ম তারিখটা একটা আইডেন্টিটি বলে বিবেচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইডেন্টিটি। কোন কোন ক্ষেত্রে নামের চেয়েও জন্ম তারিখ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে কাউকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে। কেননা, নানান কারণে মানুষের নাম বদলায় (বিয়ের পর, ডিভোর্সের পর, অন্য দেশ থেকে এসে সহজে মনে রাখা ও উচ্চারণের সুবিধের জন্যে অনেকে, যেমন, প্রায় সকল চীন দেশীয় লোকজন আমেরিকাতে এসে, অফিসিয়ালি নাম বদলে এদেশের খুব পরিচিত নাম গ্রহণ করে)। নাম বদলানোর প্রক্রিয়াটিও খুব সহজ এখানে। কিন্তু আমেরিকান সংস্কৃতিতে কারো জন্ম তারিখ কখনো বদলায় না যেহেতু প্রতিটি জন্ম সতর্কভাবে রেকর্ড করা হয় জন্মলগ্নেই, এবং জন্ম তারিখ ছাড়াও বার্থ সার্টিফিকেটে লেখা থাকে মা-বাবার নাম । জন্ম তারিখকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবার যুক্তি হলো, দুটো মানুষের এক নাম হোতে পারে। কিন্তু এক নামের মানুষ দুটোর এক-ই দিনে জন্মের তারিখ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা নয়। খুব কম সময়েই তা ঘটে।
হুমায়ূনের জন্ম সাল হিসেবে ১৯৫০-এর বদলে প্রায় সর্বত্র-ই ১৯৪৮-এর ব্যবহার দেখে বোঝা যায়, আমাদের দেশের অন্যদের মতো বয়স কমাবার দিকে আগ্রহ ছিল না হুমায়ূনের। স্কুলের কাগজে যা-ই লেখা থাক না কেন, হুমায়ূন নিজে তার সঠিক জন্ম তারিখটাই সর্বত্র ব্যবহার করতেন, অন্তত বাংলাদেশে। তাঁর বইপুস্তকের ফ্ল্যাপে - জন্মদিনের উৎসব পালনে। এটাতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন হুমায়ূন যে স্লোন ক্যাটারিং হাসপাতালে কিমো দেবার আগে নিশ্চিত হবার জন্যে যখন তাঁর নাম ও জন্মতারিখ জিজ্ঞেস করা হতো একেবারে শেষ মুহূর্তে, অভ্যেস মতো হুমায়ূনের নিজের মুখে দিয়ে সহজেই উচ্চারিত তাঁর জন্ম তারিখ শুনে নার্স ওষুধ হাতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তো। ভুল রোগীকে কিমো দিতে এসেছে ভেবে কাগজপত্র ঘাঁটাঘটি শুরু করে দিত। তখন নিজের ‘ভুল’ টের পেয়ে আবার নার্সকে ডেকে প্রকৃত সত্যটা বুঝিয়ে অফিসিয়াল জন্ম তারিখটা দিতে হতো তাঁর। হুমায়ূনের অফিসিয়াল জন্ম তারিখ ১৯৫০ সালের ১০ এপ্রিলে। আর আসল জন্ম তারিখ ১৯৪৮ সালের ১৩ নবেম্বর। হুমায়ূনের জন্মের ঠিক ২৯ বছর পরে আমার প্রথম সন্তান, কন্যা জয়ীষার জন্ম হয়, ১৯৭৭ সালের, সেই ১৩ নবেম্বরেই। তবে মজার ব্যাপার হলো হুমায়ূনের মতো আমার-ও দুটি জন্ম তারিখ। আর আশ্চর্য, সেই দু’টি জন্ম সাল ঠিক হুমায়ূনের-ই জন্ম সাল, অর্থাৎ ১৯৪৮ আর ১৯৫০-এ। প্রথমটি মানে ১৯৫০, হুমায়ূনের মতো-ই, আমার-ও স্কুলে দেওয়া জন্ম সাল, মানে এসএসসি সার্টিফিকেটের জন্ম সাল। আর ১৯৪৮ হলো সেই জন্ম সাল যেটা আমি পরে সংশোধন করে ব্যবহার করতে শুরু করেছি। কিন্তু আরো পরে জানতে পেরেছিলাম, সেটাও, মানে ১৯৪৮ -ও সঠিক ছিল না। তার মানে দুটো-ই ভুল। অনেক পরে বাবার অফিসের ডায়রি থেকে আবিস্কৃত হয়েছে, আমার প্রকৃত জন্ম তারিখ। এই দুটোর মাঝামাঝি। মোট কথা, আামি ও হুমায়ূন সমবয়সী হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে হুমায়ূন আমার চেয়ে এক ক্লাস নিচে পড়তেন। দু’জনেই বিজ্ঞানে, আমি ফার্মেসীতে, হুমায়ূন কেমিস্ট্রিতে। সমবয়সী বলেই জীবনের বেলাশেষে দেখা হলেও প্রথম দিন থেকেই আমরা পরস্পরকে নাম ধরে-ই ডাকি।
তাঁর বেশির ভাগ নাতিদীর্ঘ উপন্যাসের গল্পগুলো যেমন, বর্ণনা যেমন, পাত্রপাত্রী ও তাদের কথাবার্তা যেমন, ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু দেখেছি হুমায়ূন আহমেদ নিজেও তেমনি সহজ, সরল, সাদাসিধে, প্রাণখোলা হাসিখুশি একজন মানুষ, যিনি গল্প করতে, হাসিতামাসা করতে, কৌতুক করতে, অর্থাৎ লোককে হাসাতে, আনন্দ দিতে প্রকৃত-ই পছন্দ করতেন। একটি গল্প বা জোক একবার বলার পরে যদি নিজের কাছে তা ভাল লাগতো, তাহলে তিনি প্রতিনিয়ত সেটা পাল্টাতেন আরো শ্রুতিশীল, আরো মজাদার করার জন্যে। আলাপে, ব্যবহারে কোনরকম কপটতা নেই, ভান নেই, উচ্চমার্গে কথাবার্তা বলে অন্যদের মোহিত করার বাসনা নেই। নেই কোন সখ নিজের ধারালো জ্ঞান, সযতেœ চর্চিত শব্দাবলী দিয়ে সুনিপুণভাবে গঠিত যুক্তিপূর্ণ বাক্য, অথবা প্রখর বুদ্ধি দিয়ে আশেপাশের অন্যদের কুপাকাৎ করে ফেলা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাÑ বোকা বানানোÑ এক কথায় অন্যদের হেয় করার অপ্রতিরোধ্য ও পরিচিত সেই মানসিকতা। হুমায়ূন যা ভাবছেন, যা তার মনে আসছে, বিশ্বাস করছেন, কথা হয়ে তা-ই ফুটে ওঠে তার মুখ থেকেÑ যেমন বেরিয়ে আসে তা অনায়াসে তার কলমের কালিতেও। অন্যরা কী শুনতে চায় তা বলার দিকে কোন ঝোঁক নেই তাঁর, লোকে কী ভাবে তাকে, তার লেখাকে, তা নিয়ে নেই কোন মাথাব্যথা কিংবা একফোঁটা দুশ্চিন্তা। এ কেমন বুদ্ধীজীবী, এ কেমন সৃজনশীল ব্যক্তি, এ কেমন খাপছাড়া বাঙালি লেখক আমাদের দেশে? অথচ, যে জানে তাকে, অনায়াসে বলতে পারবে নিজের ওপর অফুরন্ত বিশ্বাস তার; – পূর্ণ আস্থা তার নিজের লেখার ক্ষমতায়।
সবশেষে বলবো, যত বড় লেখক আর যত রেকর্ড ভঙ্গকারী সৃজনশীল ব্যক্তিত্যের অধিকারী-ই হোন না কেন হুমায়ূন আহমেদ, ব্যক্তি জীবনে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঘরোয়া প্রকৃতির একজন মানুষ। স্ত্রী-পুত্রদের জড়িয়ে জাপটে ঘরের ভেতর বসে সময় কাটাতে তার ক্লান্তি হতো না। এমন কি এত যে তিনি লিখে গেছেন, তার প্রায় সব-ই নিজের ঘরে বসে লেখা। অন্য লেখকদের মতো লেখক-সঙ্গ-আড্ডা-তর্ক বা ঘরের বাইরে কোন নিরিবিলি জায়গার তার দরকার হতো না লেখায় একাগ্রতা আনার জন্যে, কিংবা চিন্তা করার জন্যে। হুমায়ূন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন কাগজ কলমে নিজের হাতে লিখতেন। কম্পিউটারে টাইপ করে তিনি কখনো লিখতেন না। লেখক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন নিভৃতচারী, প্রায় একলা। ফুটফুটে দুই শিশু পুত্র, নিষাদ নিনিদ, যাদের দুজনের মুখমণ্ডলেই হুমায়ুনের মুখের সাদৃশ্য ঈর্ষণীয়ভাবে উপস্থিত, কখনো পেটে, কখনো ঘাঁড়ে , কখনো পিঠে বা মাথায় চড়ে বাবার উপস্থিতি সর্বক্ষণ উপভোগ করতো। আর হুমায়ূণ? চারদিকে সবকিছু ঠিকঠাকমতো থাকা সত্বেও, সব ফেলে, সব ভুলে, ক্ষণে ক্ষণেই ডেকে উঠতেন তার প্রিয়তমা পতœীর উদ্দেশে, বেশ জোরেই, “কুসুম, কুসুম” বলে। শাওন হয়তো তখন নিনিদের জন্যে খাবার তৈরি করছে, অথবা ইন্টারনেটে হিউস্টনের সেই বিশেষ হাসপাতালে শেষ পর্যায়ের ক্যন্সারের রোগীর জন্যে অল্টারনেটিভ মেডিসিন প্রয়োগ করে নতুন কী সফলতা পেয়েছে জানার চেষ্টা করছে, ঘরের আরেক প্রান্তে বসে বসেই। অনুক্ষণ চোখে হারানো, হৃদয়ে দোল দেওয়া তার “কুসুম”-ও তখন সব কাজ, সব দায়িত্ব ফেলে হাসি মুখে ছুটে আসতো হুমায়ূনের কাছে, ‘এই তো আমি, কী চাও? কিছু দেব?’
না, তেমন বিশেষ কিছু চান না হুমায়ূন। কেবল শাওনকে কাছে চান। তার পাশে। পারলে সর্বক্ষণ।




